
শেখ রোকন॥ ব্রিটিশ সাময়িকী ‘দ্য ইকোনমিস্ট’ তাদের বর্ষশেষ ও বর্ষশুরু সংখ্যায় (২১ ডিসেম্বর ২০২৪-৩ জানুয়ারি ২০২৫) বাংলাদেশকে বিদায়ী বছরের ‘কান্ট্রি অব দ্য ইয়ার’ ঘোষণা করে বলে ‘ইন ২০২৫ ইট উইল নিড টু রিপেয়ার টাইজ উইথ ইন্ডিয়া’। নতুন বছরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ‘মেরামত’ যদি অগ্রাধিকার হয়, সেখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে আন্তঃসীমান্ত নদীর ব্যাপারে ঐকমত্য। বলা বাহুল্য, বিষয়টি সহজ নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষায় সম্পর্কের ‘সুবর্ণ অধ্যায়’ চলাকালে এবং বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় ‘সবকিছু দিয়ে দেওয়া’ সত্ত্বেও গত দেড় দশকে যেখানে কার্যকর সমঝোতা সম্ভব হয়নি, সেখানে কার্যত মুখদর্শন অনুপযোগী সময়ে কী অর্জন সম্ভব? ফলে নতুন বছরে অনিবার্যভাবেই আন্তঃসীমান্ত নদীবিষয়ক সমঝোতার ক্ষেত্রে আমার বিবেচনায় অন্তত ৫টি চ্যালেঞ্জ থাকছে।
এক. গঙ্গা চুক্তির নবায়ন
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত দাপ্তরিকভাবে স্বীকৃত ৫৪ বা রিভারাইন পিপলের গবেষণামতে ১২৩ আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে এখন পর্যন্ত কার্যকর সমঝোতা বলতে সবেধন নীলমণি ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি। যদিও ২০১৯ সালের অক্টোবরে ফেনী এবং ২০২২ সালে সেপ্টেম্বরে কুশিয়ারা নিয়ে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, প্রবাহ ও প্রভাব তুলনায় সেগুলো গঙ্গার তুল্য হতে পারে না। তুলনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে; ফেনী চুক্তিতে পানির পরিমাণ ১ দশমিক ৮২ কিউসেক, কুশিয়ারায় ১৫৩ কিউসেক, আর গঙ্গায় অন্তত ৩৫ হাজার কিউসেক পানি ভাগাভাগির প্রশ্ন। গঙ্গা চুক্তিতে ভাটির দেশের অধিকার ও ন্যায্যতা কতটা সুরক্ষিত, সেই প্রশ্ন যদিও প্রথম থেকেই ছিল; আসন্ন শঙ্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে এর নবায়ন। ২০২৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তিটির কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাবে।
দেখা যাচ্ছে, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির নবায়ন নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আলোচনা হয়নি। যেমন ২০২৪ সালের ২২ জুন সর্বশেষ বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতির ৬ নম্বর দফায় বলা হয়, “১৯৯৬ সালে সম্পাদিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি নবায়নের জন্য গঠিত যৌথ কারিগরি কমিটি আলোচনা শুরু করার বিষয়টিকে আমরা স্বাগত জানাই।’’ দেখা যাবে, আগের তিন বছরের বৈঠকের পরও গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি নবায়ন বিষয়ে যৌথ বিবৃতির ভাষ্যও কমবেশি অভিন্ন। ২০২২ সালে বরং চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত পানির ‘সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার’ করার কথা বলে কার্যত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চুক্তি নবায়ন দূর কি বাত; নবায়নবিষয়ক ‘ঝুলন্ত’ আলোচনা শুরু করা যাবে কিনা, সেটিই ২০২৫ সালের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকছে। বিস্তারিত পড়ুন– ‘গঙ্গা চুক্তির নবায়ন ২০২৬ সালের মধ্যে সম্ভব?’ (সমকাল, শেখ রোকন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)।
দুই. তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি
তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তিবিষয়ক আলোচনা সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন; ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সূচিত হয়েছিল। এরপর তিস্তা অববাহিকায় পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে; স্বাধীন সিকিম ভারতে যোগ দিয়েছে; কিন্তু নদীটি নিয়ে আলোচনা শেষ হয়নি। তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে ‘সম্পূর্ণ প্রস্তুত’ একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এসেছিলেন। শেষ মুহূর্তে দৃশ্যত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগড়ায় সেটি ভেস্তে যায়। যদিও এই ভাষ্য নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তারপর থেকে গত ১৩ বছরে ভারতের দিক থেকে একের পর এক প্রতিশ্রুতি এসেছে, চুক্তি সম্ভব হয়নি। ভারতের বারংবার প্রতিশ্রুতিভঙ্গে হতাশ বাংলাদেশ তিস্তা অববাহিকায় চীনের সহায়তায় যে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছিল, সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুনে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে সেটিও নাকচ হয়ে গেছে।
ওই বৈঠকের পর দুই পক্ষের ‘অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি’ সংক্রান্ত ঘোষণার ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়, ‘উন্নয়ন সহযোগিতার অংশ হিসেবে পারস্পরিক সম্মত সময়সীমার মধ্যে ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমরা তিস্তা নদীর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাগত উদ্যোগ গ্রহণ করব।’ পাশাপাশি বলা হয়, ভারতের একটি কারিগরি প্রতিনিধি দল তিস্তার সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বাংলাদেশ সফর করবে। এর মধ্য দিয়ে তিস্তার পানি বণ্টন ইস্যু বা বিকল্প হিসেবে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, দুটোকেই কার্যত হিমাগারে পাঠানো হয়। এমনকি পানি বণ্টনের বদলে যৌথ অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনাও নাকচ হয়ে যায়; কারণ ভারত তিস্তা নিয়ে যা করার করতে চায় ‘বাংলাদেশের অভ্যন্তরে’। বিস্তারিত পড়ুন– ‘তিস্তা পরিস্থিতি তাহলে কী দাঁড়াল?’ [সমকাল, শেখ রোকন, ২৪ জুন ২০২৪]।
তিন. ব্রহ্মপুত্রে চীন-ভারতের মেগাড্যাম
বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও প্রতিবেশগত দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী ব্রহ্মপুত্র, যমুনা। কারণ, আন্তঃসীমান্ত নদীগুলো দিয়ে যে প্রবাহ আমরা পাই, এর ৬৫ শতাংশই আসে এই নদী দিয়ে (সিএনএ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সল্যুশন, ২০১৬, ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র)। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নিয়েই আমাদের আলোচনা ও উদ্বেগ যেন সবচেয়ে কম। এর একটি কারণ গঙ্গা, তিস্তা বা অন্যান্য নদীর মতো ব্রহ্মপুত্রে ভারতীয় ব্যারাজ বা ড্যাম নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেবল বাংলাদেশ নয়, ভারতেরও কপালে ভাঁজ ফেলেছে সাংপো নামে তিব্বতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের উজানের অংশে চীনের একাধিক ড্যাম নির্মাণের খবর। বাংলাদেশের জন্য বাড়তি উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, আমাদের ব্রহ্মপুত্রে মূল প্রবাহ আসে অরুণাচল ও আসামের যে বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চল থেকে, সেখানেও সুবনসিড়ির মতো কিছু উপনদীতে ভারতও ইতোমধ্যে ড্যাম নির্মাণ করছে। আবার চীনা মেগাড্যামের ‘প্রতিক্রিয়া’ হিসেবেও এখন ব্রহ্মপুত্রের অরুণাচল অংশ বা ‘সিয়াং’ নদীতে মেগাড্যাম নির্মাণ করতে চাইছে ভারত। তার মানে, ব্রহ্মপুত্রে চীনা মেগাড্যামের গোদের ওপর যুক্ত হচ্ছে ভারতীয় মেগা ড্যামের বিষফোড়া। বিস্তারিত পড়ুন- চীন-ভারতের ‘পানি অস্ত্র’ এবং বাংলাদেশের করণীয় (সমকাল, শেখ রোকন, ২০ অক্টোবর ২০২৪)।
২০২৫ সাল ও পরবর্তী বছরগুলোতে তাই অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটি। মনে রাখা জরুরি, গঙ্গাবিষয়ক সমঝোতা না থাকার অর্থ বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত প্রবাহের কমবেশি ১৫ শতাংশে বিরূপ প্রভাব; আর ব্রহ্মপুত্র নিয়ে অবিলম্বে সমঝোতা সম্ভব না হলে ঝুঁকিতে থাকবে কমবেশি ৬৫ শতাংশ! বাংলাদেশের পানিসম্পদ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার জন্য এর চেয়ে বিপর্যয়কর আর কী হতে পারে?
চার. ভারতের নদীসংযোগ প্রকল্প
ভারতের ‘ন্যাশনাল রিভারলিঙ্কিং প্রজেক্ট’ বা নদীসংযোগ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশের বেশ সোচ্চার ভূমিকা দেখা গিয়েছিল একুশ শতকের শুরুতে; কূটনৈতিক বার্তা, সভা-সমাবেশ, লংমার্চ, লেখালেখি সহযোগে। কারণ ওই সময়ে ভারতীয় সরকার, উচ্চ আদালত, এমনকি পরিবেশবাদীরাও ওই প্রকল্পের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে কেবল নয়; ভারতের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের প্রবল প্রতিবাদের মুখে প্রকল্পটির প্রধান দুটি অংশের মধ্যে ‘হিমালায়ান’ বা হিমালয় অঞ্চলের ‘বাস্তবায়ন থামিয়ে দেয়’। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরের যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, আমাদের সুরমা-কুশিয়ারা অববাহিকায় বিরূপ প্রভাব হলে মণিপুরে তিপাইমুখ ড্যাম হবে না। এসব কারণে বাংলাদেশের সোচ্চার ভূমিকা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে থিতিয়ে এলেও ভারত থেমে নেই। বরং কিছু ‘ক্যামোফ্লাজ প্রজেক্ট’ বা ছদ্ম প্রকল্প গ্রহণ করে; যাতে সেগুলোকে নদীসংযোগ প্রকল্পের অংশ মনে না হয়।
যেমন, গঙ্গায় আমরা কেবল পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কা ব্যারাজের কথা জানি। কিন্তু ২০১৭ সালের মার্চে ঢাকা ট্রিবিউনে প্রকাশিত এক ‘ভূমিধস’ প্রতিবেদনে আমাদের বন্ধু ও সহযোদ্ধা আবু বকর সিদ্দিক দেখিয়েছিলেন, আরও উজানে বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে অন্তত ২৯টি ‘ছোট’ ড্যাম বা ব্যারাজ রয়েছে। ফারাক্কার পানি প্রত্যাহার ক্ষমতা যেখানে সর্বোচ্চ ৮০ হাজার কিউসেক, এগুলোর সম্মিলিত পানি প্রত্যাহার ক্ষমতা সেখানে অন্তত ২ লাখ ৯২ হাজার কিউসেক। তার মানে, গঙ্গার ছোট ছোট ড্যাম ও ব্যারাজগুলো আলোচনার বাইরে থেকেই ফারাক্কার তিন গুণের বেশি পানি প্রত্যাহার করছে! একইভাবে তিস্তার পানিও মহানন্দা হয়ে আরও পশ্চিমে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে নদীসংযোগ প্রকল্প নাম না দিয়েই।
যেমন, ২০২১ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা দিয়েছিলেন, কথিত বন্যা মোকাবিলায় ৫ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে জলাভূমি ও নদীর দিকে বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্রের ‘উদ্বৃত্ত প্রবাহ’ ঘুরিয়ে দিতে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ‘ইসরো’ এবং নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার ‘নেসাক’ কাজ সম্পন্ন করেছে। (এনডিটিভি অনলাইন, ২৫ জুলাই, ২০২১)। এখানে নদীসংযোগের নামগন্ধ নেই; কিন্তু কাজ একই।
বাংলাদেশ-ভারত ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক’ বিবেচনায় এতদিন নদীসংযোগ প্রকল্পের সর্বনাশ এভাবে তলে তলে করা হলেও ২০২৫ সাল থেকে তা নাও থাকতে পারে। আমার আশঙ্কা, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আগের চেয়ে জোরেশোরে ও প্রকাশ্যে নদীসংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে দিতে পারে। সেটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে।
পাঁচ. রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচের অহেতুক অভাব
নদ-নদীর ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা যখন পথ হারায়, যেমনটি বাংলাদেশ-ভারতের ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং সামনের দিনগুলোতে আরও প্রকট হবে; তখন ভাটির দেশের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো। বাংলাদেশের সামনে রয়েছে দুটি এমন রক্ষাকবচ। প্রথমটি সংক্ষেপে ‘জাতিসংঘ পানিপ্রবাহ সনদ, ১৯৯৭’ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টিকে সংক্ষেপে বলা যায় ‘জাতিসংঘ পানি সনদ, ১৯৯২’। দ্বিতীয়টি নানা দিক থেকে প্রথমটির চেয়ে সহজ, কার্যকর ও সুবিধাজনক। (আগ্রহীরা পড়ুন, হেলায় ফেলে রাখা আন্তর্জাতিক রক্ষাকবচ; সমকাল, ১৩ অক্টোবর ২০২১)।
আক্ষেপের বিষয়– বাংলাদেশ এর কোনোটিকেই এখন পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারেনি বা চায়নি। রিভারাইন পিপলসহ বাংলাদেশের নদী ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অনেক বছর ধরেই এসব রক্ষাকবচ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনের জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছে। কিন্তু বিএনপি, আওয়ামী লীগ, ওয়ান ইলেভেন, অন্তর্বর্তী– কোনো সরকারের দিক থেকেই কার্যকর উদ্যোগ নেই! ২০২৫ সালেও যদি এগুলো নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার দোটানায় থাকে, এর চেয়ে হতাশাজনক আর কিছু হতে পারে না। বিস্তারিত পড়ুন– তিস্তা নিয়ে ‘নরম-গরম’ কথার বাইরেও যা করতে হবে (সমকাল, শেখ রোকন, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।
ওপরে নতুন বছর বা পরবর্তী সময়ে আন্তঃসীমান্ত নদী নিয়ে যে চারটি চ্যালেঞ্জের কথা বলেছি, সেগুলো উতরানোর জন্য মোক্ষম অস্ত্র হতে পারত আলোচ্য দুই আন্তর্জাতিক রক্ষাকবচ। কিন্তু স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষরের প্রশ্নে বাংলাদেশের সব সরকারেরই বোধগম্য দ্বিধা, মোক্ষম অস্ত্র দুটিকেই পরিণত করেছে আরেকটি চ্যালেঞ্জ।
লেখক: নদী গবেষক










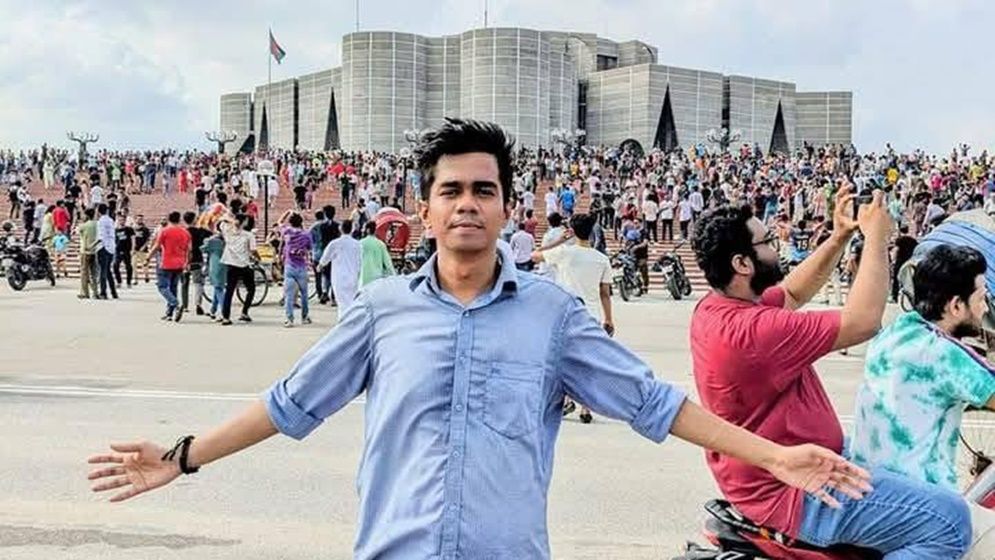











আপনার মতামত লিখুন :